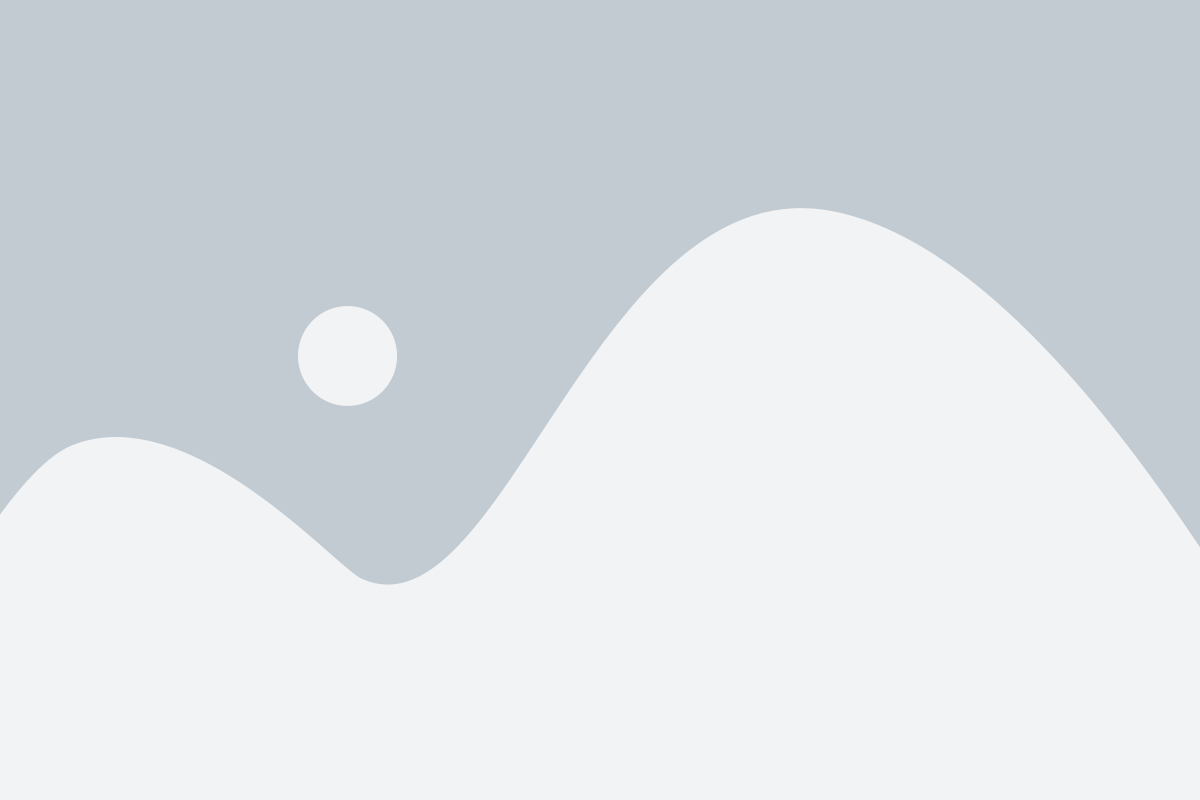ব্রিটেনে বিক্রি হবে কলকাতার টাটকা রসগোল্লা, কাঁচামাল নিয়েই রয়েছে জট!!
মানবতার হাহাকার!!

ধনীরা আরও ধনী হচ্ছেন,গরিবরা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন-ধনই বাক্যটা আজ হচ্ছেন কোরিকরা জনে অদশ্য হয়ে যাচ্ছেন পরিসংখ্যানের নিমর্ম সত্য। জি ২০ প্রকাশিত সদ্যতম রিপোর্টটি প্রমাণ করে দিয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতি আজ আর ‘উন্নয়ন’-এর নয়, ‘অসাম্য’র যাত্রাপথে চলছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ়-এর নেতৃত্বে গঠিত যে বিশেষজ্ঞ কমিটি এই রিপোর্টটি তৈরি করেছে, তারা স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়েছেন।
বিশ্বজোড়া বৈষম্য এখন ‘আপৎকালীন স্তরে’ পৌঁছে গিয়েছে।২০০০সাল থেকে ২০২৪এই ২৪ বছরে বিশ্বের যে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তার ৪১ শতাংশই গিয়েছে ধনীতম ১ শতাংশের হাতে।
অন্যদিকে, মানবসভ্যতার নীচের অর্ধেক অংশ-যাদের ঘামে এই সম্পদ তৈরি-তাদের ভাগে এসেছে মাত্র ১ শতাংশ।এই পরিসংখ্যান শুধু অর্থনৈতিক নয়, নৈতিক দেউলিয়াপনার দলিল। মানুষ আজ আর সমাজের অংশ নয়, বাজারের পণ্য। বৈষম্যের দৌড়ে ভারতও পিছিয়ে নেই। রিপোর্ট বলছে, ২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতের ধনীতম ১ শতাংশের সম্পদ বেড়েছে ৬২ শতাংশ।
অর্থাৎ, দেশের অর্থনীতির সিংহভাগই আটকে গেছে কিছু শিল্পপতি ও কর্পোরেট গোষ্ঠীর মুঠোয়। এই প্রবণতা কেবল সংখ্যার নয়, এটি ক্ষমতার প্রশ্নও-কারণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ যখন অল্প হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন গণতন্ত্রের ভিত কেঁপে ওঠে। এই পরিসংখ্যান যেন আয়নার মতো। একদিকে ‘বিকাশ’ ও ‘নতুন ভারতের’ স্লোগান, অন্যদিকে কর্মহীন যুবসমাজ, কৃষকের আত্মহত্যা, ও মধ্যবিত্তের ঋণ-জর্জর জীবন। এক দেশে যখন বিলাসবহুল গাড়ির বিক্রি রেকর্ড ছুঁয়েছে, তখন অন্য দেশে হাসপাতালে বেড না পেয়ে মানুষ মরছে।
এই ব্যবধানই আজকের ভারতের সত্যিকারে বিভাজনরেখা- ধর্ম নয়, সম্পদ। বিশ্বায়নের নামে যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তা এখন পুঁজি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্র এখন বাজারের দাস, আর সরকার পরিণত হয়েছে কর্পোরেট বিজ্ঞাপন সংস্থায়।
নীতি তৈরি হচ্ছে সেই সব গোষ্ঠীর সুবিধামতো, যারা নির্বাচনি তহবিল দেয়, নীতি নির্ধারণের ‘নির্দেশনা’ দেয়। বৈষম্যের প্রশ্ন তাই কেবল অর্থনীতির নয়, এটি গণতন্ত্রেরও সংকট। জি-২০ রিপোর্টে অথার্থই বলা হয়েছে- যেসব দেশে আয়বৈষম্য তীব্র, সেখানে কাণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের আশঙ্কা ৭ গুণ বেশি।এটিই ইতিহাসের নিয়ম-যেখানে সমাজে আস্থা ভাঙে,সেখানে গণতন্ত্র টিকে না।দারিদ্র্যের চেহারা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু মুছে যাচ্ছে না।আজ বিশ্বজুড়ে ২৩০ কোটি মানুষ নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা পান না।২০১৯ সালের তুলনায় ৩কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষ নতুন করে ক্ষুধার্তের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন।
স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় ১৩ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিয়েছে।অর্থাৎ, প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, মানুষ ততই পিছিয়ে পড়ছে জীবনের নিশ্চয়তার।
এ যেন সভ্যতা কফিনে বিলাসের সোনার পেরেক। স্টিগলিজ্জ কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী, ‘ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ইনইক্যুয়ালিটি (IPI)’ নামের এক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে বৈষম্য পর্যবেক্ষণ ও নীতি পরামর্শ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- যে বিশ্বব্যবস্থা নিজেই পুঁজির সেবক, সেখানে এমন কোনও সংস্থা কি সত্যিই কার্যকর হবে? যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে কর্পোরেট লবি কাজ করে, সেখানে ‘সমতা’ শব্দটা কি নিছক এক স্লোগান হয়ে থাকবে না?
ভারতে আজ অর্থনৈতিক বৈষম্য কেবল অর্থনীতির বিষয় নয়, এটি এক সামাজিক অন্যায়।শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান-সব ক্ষেত্রেই ধনীদের জন্য সুবিধা,গরিবের জন্য কষ্ট।
রাষ্ট্রের করনীতি ধনীদের রেহাই দেয়, অথচ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের ঘাড়ে চাপায় জিএসটি, জ্বালানির দামে মুনাফা, ঋণের সুদ।অর্থাৎ, সরকার আজ ‘জনতার’ নয়- ‘পুঁজির’ সরকার। বৈষম্য শুধু পরিসংখ্যান নয়, এটি নৈতিক ব্যর্থতা। এই রিপোর্ট কেবল একটি অর্থনৈতিক নথি নয়- এটি সভ্যতার বিবেক পরীক্ষা।এক পৃথিবীতে, যেখানে ১ শতাংশ মানুষের কাছে ৪১ শতাংশ সম্পদ, আর অর্ধেক মানুষ প্রতিদিনের খাবারের জন্য সংগ্রাম করে-সেখানে উন্নয়নের বড়াই করা একপ্রকার নিষ্ঠুরতা।আজ সময় এসেছে প্রশ্ন করার- উন্নয়ন কাদের জন্য? যদিও উত্তর হয় অল্প কয়েকজনের জন্য, তবে বুঝতে হবে- আমরা কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যের নয়, নৈতিক দেউলিয়াপনার যুগে প্রবেশ করেছি। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রকে এখন এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে-সমতা ছাড়া উন্নয়ন টেকে না. আর বৈষম্য নিয়ে গণতন্ত্র বাঁচে না।