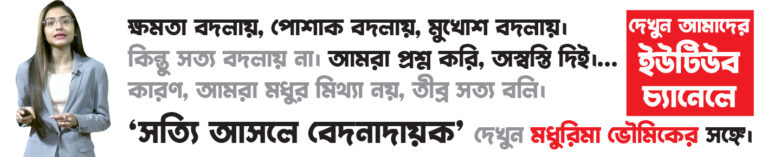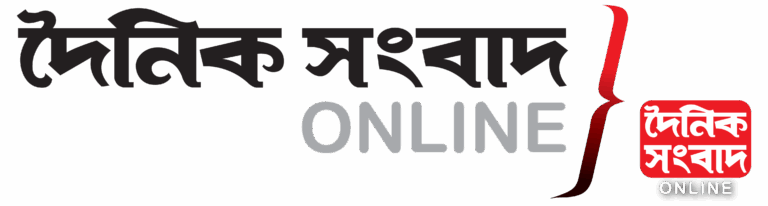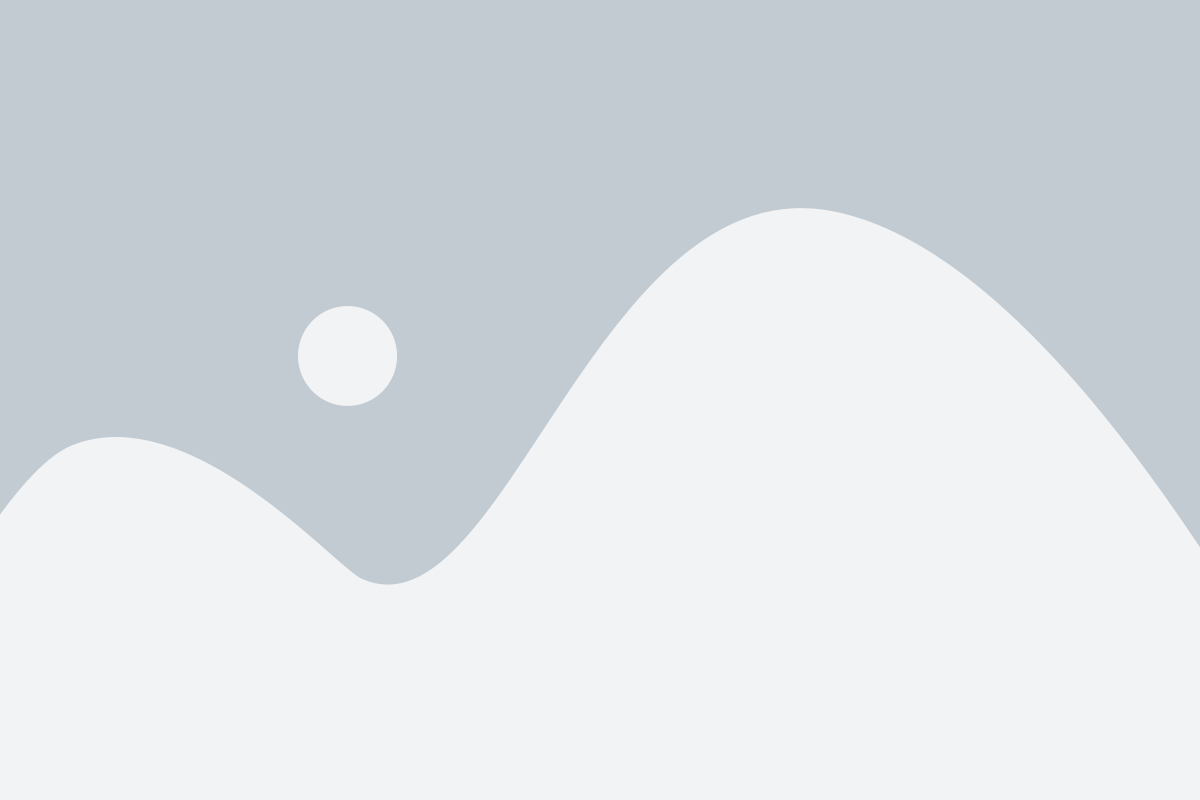চিনের কৌশলী আলিঙ্গন!

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন চিন সফর কেবলমাত্র কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এক গভীর অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এবং ভূকৌশলগত বাস্তবতার প্রতিফলন। সাত বছর আগে সীমান্তে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে দুই দেশের সম্পর্কে তিক্ততা জন্মেছিল, আজ সেই অবস্থান থেকে এক নতুন সমীকরণ তৈরির প্রয়াস চলছে। এই পরিবর্তনের মূল কারণ বন্ধুত্ব নয়, বরং অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কঠোর বাস্তবতা। তাই এ মাসের অন্তিম দিনে তিয়ানজানে এসসিও সম্মেলনের পার্শ্ববৈঠকে মোদি ও শি জিনপিং মুখোমুখি হলে সেটি হবে নিঃসন্দেহে অতীব ইঙ্গিতবাহী, বিশেষ করে ওয়াশিংটনের শুল্ক বাণের পরিমণ্ডলে।
মে মাসে ‘অপারেশন সিন্দুর’-এর সময় পাকিস্তানকে যেভাবে চিন সামরিক সহায়তায় ভরে দিয়েছিল সীমান্ত পেরিয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে সরঞ্জাম সরবরাহ পর্যন্ত, তা ভারতের কাছে স্পষ্ট বার্তা ছিল। অথচ সেই ঘটনার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণটি সহজবোধ্য। আমেরিকার শুল্ক যুদ্ধ ও প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞায় চিনের রপ্তানি বাজার ধাক্কা খেয়েছে, সরবরাহ শৃঙ্খলে চাপ তৈরি হয়েছে এবং বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থায় ভারত নামক এক বিপুল বাজার ও উৎপাদন ক্ষেত্রকে উপেক্ষা করা বেজিংয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।
সম্প্রতি কিছু পদক্ষেপ তারই প্রতিফলন। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি উড়ান পুনরায় চালুর সম্ভাবনা, কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা খোলার আলোচনা এবং সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আংশিক ঐকমত্য সবই সেই নতুন বাস্তবতার অঙ্গ। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের দিল্লী সফর এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে বিনিয়োগ। গলওয়ানের পর ভারত সরকার যে কঠোর অনুমোদন প্রক্রিয়া চাপিয়ে দিয়েছিল চিনা মূলধনের উপর – যাতে প্রতিটি প্রস্তাব গভীরভাবে যাচাই ছাড়া অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হতো না, চিন এখন সেটি শিথিল করার দাবি তুলেছে। খবর ইঙ্গিত দিচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময়ই হয়তো এই নিয়ম শিথিল হতে চলেছে। ফলে কৌশলগত কিছু ক্ষেত্র বাদ দিলে বাকি জায়গায় চিনা বিনিয়োগ নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারবে।
এখানেই ভারতের দ্বিধা প্রকট। একদিকে দেশের উৎপাদন খাত দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের সহজ বিনিয়োগ প্রবাহের দাবি জানিয়ে আসছে, কারণ সস্তা কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ এবং দ্রুত সরবরাহের ক্ষেত্রে চিনের তুলনা নেই। অন্যদিকে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন, অতিরিক্ত প্রবেশাধিকার মানে তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিকম বা শক্তি ক্ষেত্রের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি বাড়ানো। ভারতের নীতি নির্ধারকদের তাই এখন প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে- কীভাবে অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও কৌশলগত নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য রাখা সম্ভব।
এই প্রেক্ষাপটে চিনের পরেই মোদির জাপান সফরের বার্তাটিও গুরুত্ববহ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর এবং উদীয়মান প্রযুক্তি খাতে টোকিওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর পরিকল্পনা আসলে বিকল্প সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার কৌশল। ভারত যদি জাপান, আমেরিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে পারে, তবে চিনের উপর নির্ভরতা কিছুটা হলেও কমানো যাবে। এই দ্বিমুখী কৌশল-একদিকে চিনকে সীমিত সুযোগ দেওয়া, অন্যদিকে বিকল্প শক্তিশালী জোট গঠন, ভারতের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম হলেও বাস্তবসম্মত পথ।
চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-এর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে লেখা চিঠি এই সমীকরণ আরও স্পষ্ট করে। মার্চ মাসে লেখা হলেও সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা সেই পত্র বার্তায় শি সরাসরি আমেরিকার নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং ভারত-চিন সম্পর্ক দ্রুত উন্নতির উপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ চিনের মূল স্বার্থ একটাই- আমেরিকার চাপ থেকে আংশিক মুক্তি পেতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থিতিশীল রাখা।
কিন্তু ভারতের কাছে শিক্ষা অন্যরকম হওয়া উচিত। সুযোগ গ্রহণ জরুরি, বিনিয়োগ প্রবাহ ও প্রযুক্তি সহযোগিতা অর্থনীতিকে গতি দেবে, সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে। তবে প্রতিটি পদক্ষেপ শর্তসাপেক্ষ হতে হবে। স্পর্শকাতর পরিকাঠামো, তথ্যনির্ভর শিল্পক্ষেত্র এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। নইলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে।
শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই- ভারত কি চিনের কৌশলী আলিঙ্গনকে নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধির সুযোগে পরিণত করতে পারবে, না উল্টো সেই আলিঙ্গনই ফাঁদে পরিণত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করছে আগামী দশকে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান।