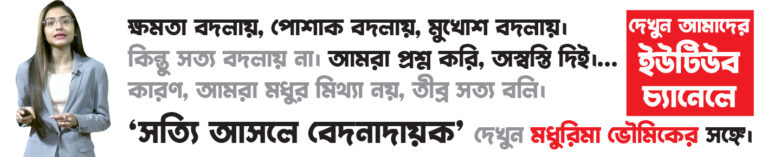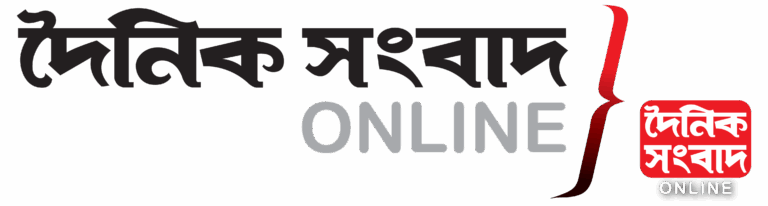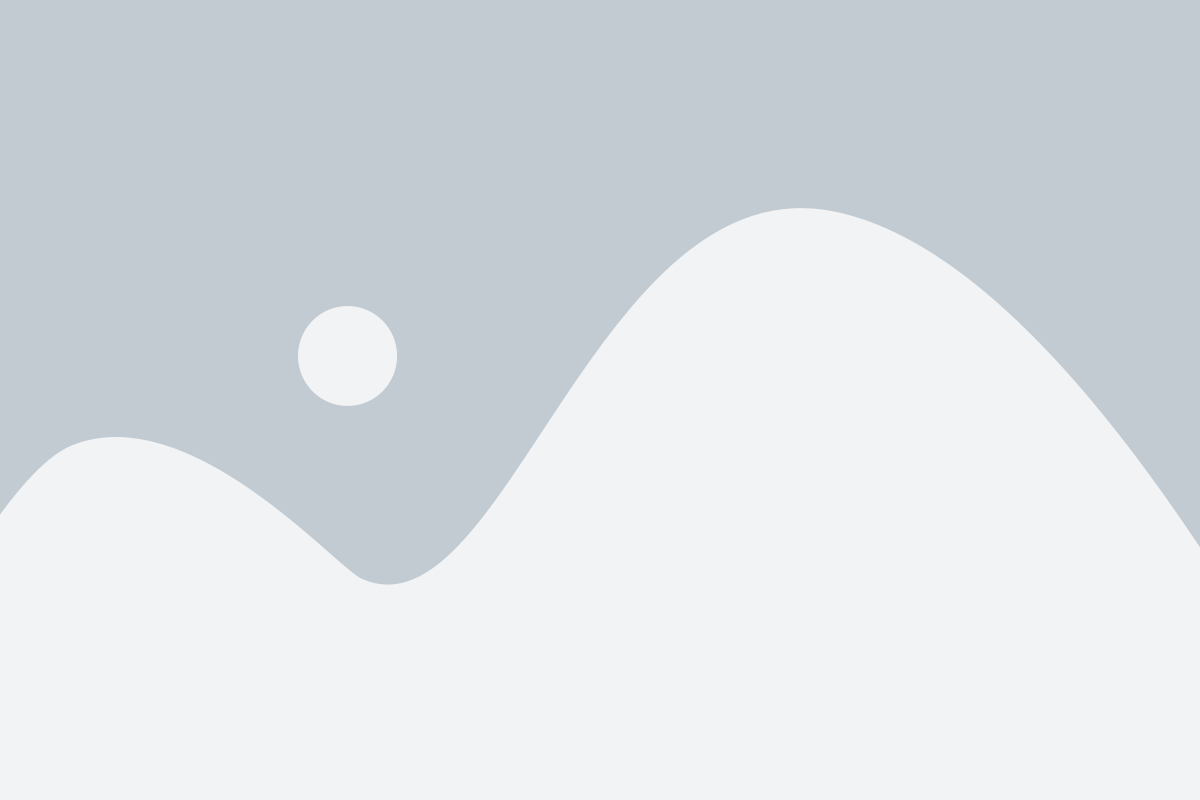জোড়া চাপে!!

আমেরিকার চড়া শুল্ক ঘোষণার অভিঘাত আপাতত বাণিজ্যের পরিসংখ্যানের কাগজে ধরা পড়ছে, কিন্তু এর প্রকৃত প্রভাব যে ভারতের রাজনীতির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। এই শুল্কবৃদ্ধি সরাসরি আঘাত করবে ভারতের ছোট ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রকে যেখানে রপ্তানি নির্ভর বহু প্রতিষ্ঠান ভরসা রাখে মার্কিন বাজারের উপর। কিন্তু সবচেয়ে বড় চাপ পড়তে চলেছে সেই সামাজিক গোষ্ঠীর উপর, যারা বিগত এক দশক ধরে মোদি সরকারের কর্পোরেট নির্ভর অর্থনীতির সর্বাধিক সুবিধাভোগী, ভারতের ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের অতি-প্রাপ্তির সৌজন্যে এ দেশের আর্থিক বৈষম্য কার্যত প্রাক-স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে নিমজ্জিত হয়েছে।
মোদি সরকারের আমলে অর্থনীতির ‘ট্রিকল-ডাউন’ তত্ত্ব কার্যত এই গোষ্ঠীকেই একচেটিয়া সমৃদ্ধ করেছে। সেই অর্থে ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতি কোনও নির্দিষ্ট তত্ত্ব নয়, এটি যুগপৎ মোহময় ও বিতর্কিত একটি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধারণা। এটি মূলত অর্থনীতির একটি চিত্রকল্প, যা দ্বারা বোঝানো হয় যে ধনীদের গড়ে তোলা সম্পদের পাহাড়ের চূড়া থেকে ফোঁটা চুঁইয়ে নামছে, শেষ পর্যন্ত তা নেমে আসছে নিম্নস্তরে, গরিবের ঘরে। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা মনে করেন, ধনী ও কর্পোরেট শ্রেণীকে যত বেশি কর ছাড়, প্রণোদনা ও ব্যবসার স্বাধীনতা দেওয়া হবে, তারা তত বেশি বিনিয়োগ করবে, সেই সূত্রে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং ধাপে ধাপে তার সুফল পৌঁছাবে সাধারণ মানুষের কাছেও। ১৯৮০-এর দশকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান ও তার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আর্থার লাফের প্রণীত ‘সাপ্লাই-সাইড ইকনোমকিক্স’ এই ধারণাকে প্রথম বাস্তবনীতির রূপ দেয়। সেই অর্থনীতির পোশাকি নাম হয়েছিল ‘রেগানোমিক্স’। তাকেই নকল করে বিরোধীরা মোদি সরকারের অর্থনীতিকে ‘মোদিনোমিক্স’ বলে কটাক্ষ করেন। এই অর্থনীতির নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, এই নীতি ধনী ও কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার জন্য এক ধরনের নৈতিক আবরণ তৈরি করে, তৈরি করে মরীচিকার মতো বিভ্রম। বাস্তবে দেখা যায়, উপর থেকে চুঁইয়ে পড়া নয়, বরং উপরের দিকেই জমা পড়ছে সিংহভাগ সম্পদ।ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক চাপিয়ে দিয়ে ঘুরপথে ব্র্যান্ড মোদির নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ককে আহত করেছেন, যে শ্রেণী ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতির সুফল ভোগ করে চলেছে।আদতে শহুরে, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী, যাদের বলা হয় ‘গেটেড কমিউনিটি’, মূলত যাদের সন্তানেরা বিদেশে পড়তে যায়, প্রমোদ ভ্রমণে যায়, আন্তর্জাতিক ব্রান্ডের প্রতি আসক্তি ইত্যাদি। এই বৃত্তটা সম্পন্ন করেছে মূলত পশ্চিমি দুনিয়া, বিশেষত মার্কিন দুনিয়ার পণ্য ও পরিষেবা। সব মিলিয়ে এই ‘লাভার্থী’ শ্রেণীর কাছে আমেরিকা যেন এক ট্রেজার আইল্যান্ড। এখন হঠাৎ ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন আলগা হয়ে পড়লে, এই শ্রেণীর সুবিধার জগৎ কেঁপে উঠবে। আর এখানেই রাজনৈতিক সমস্যার সূচনা – কারণ এরা কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, ভোটের অঙ্কেও বিজেপির উগ্র সমর্থক।
এদিকে, ঘরের ভেতরেও বাতাস ক্রমে পুরু হয়ে ঘনীভূত হচ্ছে। ভোট চোর, গদি ছোড়’ স্লোগানে উত্তাল বিরোধী শিবির ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। বাস্তবে নেমে এসেছে এমন রাজনৈতিক সংহতি, যা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের রাজনীতিতে দেখা যায়নি। সংসদীয় গরিমার বাইরে এই রাস্তার লড়াই ক্ষমতাসীন দলের জন্য বিপজ্জনক – কারণ এটি মিডিয়া-নিয়ন্ত্রিত প্রচারের সীমা ভেঙে সরাসরি জনমনে ঢুকে পড়ে। তার উপর যোগ হয়েছে ভূরাজনৈতিক কৌশলের অনিশ্চয়তা। মার্কিন শুল্ক চাপ ও আন্তর্জাতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে দিল্লীর বিদেশনীতি যদি ক্রমশ বেইজিংয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। যে উচ্চবিত্ত ভোটব্যাঙ্ক এখনও মোদির প্রতি বিশ্বস্ত, তাদের সন্তানরা চিনে নয়, বরং আমেরিকাতেই পড়াশোনা করে, কেরিয়ার গড়ে। চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাদের স্বপ্নপথে কাঁটা বিছিয়ে দেবে। এতে ক্ষোভ জমাট বাঁধা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে বাইরের চাপ ও ঘরের ভেতরের ফাটল; দুটি-ই সমানতালে বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারের টানাপোড়েন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংহতি এবং ভোটব্যাঙ্কের মনস্তত্ত্ব; এই তিনটি রেখা যদি এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়, তাহলে সেটি কেবল এক নির্বাচনি ঝুঁকি নয়, বরং ক্ষমতাতন্ত্রের সামনে প্রকৃত বিদায় – সঙ্কেত হয়ে উঠতে পারে। মোদি সরকার কি তা আঁচ করছে? নাকি এখনও বিশ্বাস করছে, জাতীয়তাবাদী বাগ্মিতা -ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারেই এই সংকট সামাল দেওয়া সম্ভব? ইতিহাস বলছে, যখন বাইরের চাপ ও ঘরের ক্ষোভ একই স্রোতে মেশে, তখন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক জাহাজও ডুবতে দেরি হয় না।