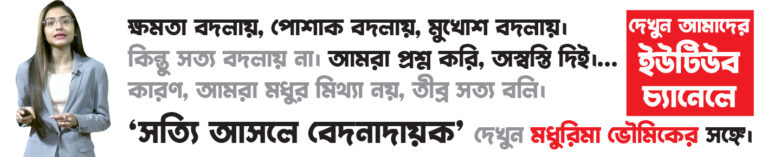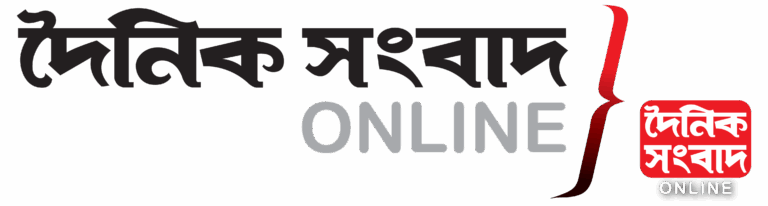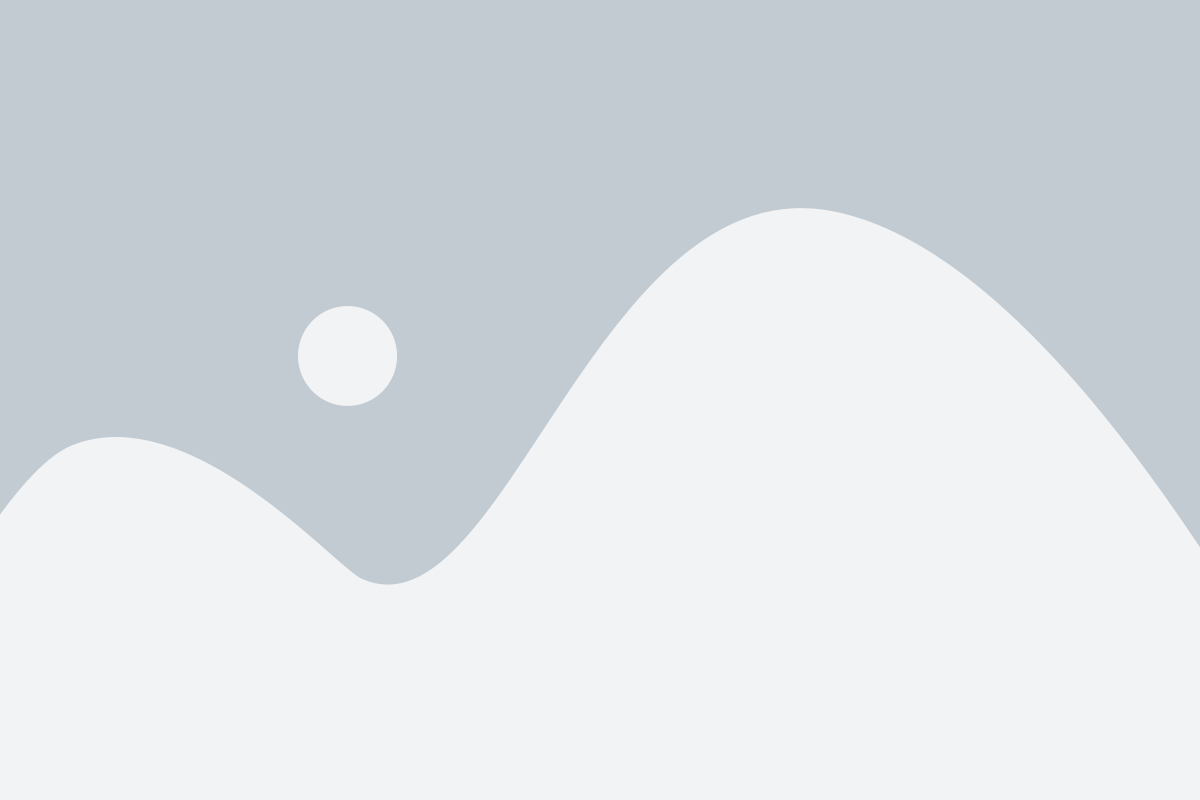শূন্যতায় দিন গোনা

বোধনের আর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে যে ব্যস্ততা আর আনন্দ উন্মাদনার শুরু হয়েছিল তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় মহানবমীর মহা আরতির সময়ে। সেই সময়ের ধূপ-ধুনো আর ঢাকের বোলের মধ্যেই হঠাৎ জেগে উঠে বিষাদ সুর। ঢাকের চটুল বোলেও ঢাকা থাকে না দশমীর বিষাদ সুর। শুরু হয় বিজয়ার আয়োজন। আনন্দ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় মানুষ। যেখানে যতটা পায় তা নিংড়ে নিয়ে উপভোগের চেষ্টা করে চলে। তাই দশমীর নিরঞ্জনের মিছিল শোভাযাত্রায়ও থেকে যায় আনন্দ আর উন্মাদনার শেষটুকু। তা দেখে মনে হবে- শেষ হইয়াও হইলো না শেষ।

দুর্গা উৎসব তাই এখনও শেষ হয়নি। চলবে আরও এক দুইদিন। এরপর শূন্য পান্ডেল দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ্মীপুজোর অপেক্ষায় এক টিমটিমে প্রদীপ জ্বালিয়ে। বুক হু হু করা এক দৃশ্য মন উদাস করে দেয়।
আবার মনের কোণে আশা জাগায়, আবার আসবে উৎসবে, আলোকোজ্জ্বল আনন্দের দিনরাত্রি। শুরু হয়ে যায় দিনগোনা। এই আমাদের নামচা। এক বুক আনন্দ- বিজয়ের, মিলনের। আর তাকে উপচে যায় এক বা একাধিক অপ্রাপ্তি আর বিষাদের ব্যথা। সব পেয়েও অপূর্ণতার এক ছোঁয়া জেগে থাকে সর্বদা। মানুষ আবার নেমে আসছেন জীবন যুদ্ধে। আনন্দ হোক আর বিষাদ- জীবন তো কোথাও থেমে থাকে না। থেকে যায় শুধু দ্বন্দ্ব। মানসিক, তাত্ত্বিক। সেই-ই জীবনকে টেনে বয়ে নিয়ে যায়। যুদ্ধদীর্ণ প্রতিটি জীবনে উৎসবমুখরতার দরকার পড়ে। জীবনের গায়ে তাই একটা বাৎসরিক প্রলেপ দেওয়া গেল। এবার আবার পথচলা। আবার লড়াই।
পৃথিবীর সব সমাজেই উৎসব আছে, থাকতে হয়। আমাদের দশভুজা বঙ্গ সংস্কৃতিতে ঘরের মেয়ে বটে। বাংলার সংস্কৃতিতে তাঁর যোগাযোগ ওতপ্রোত। তাঁর উৎস কেবল পুরাণ বা মিথ নয়। তাঁকে আমরা খুঁজে পাই ইতিহাসের নানান পরতে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতির মতো তাঁর উপস্থিতি প্রাচীন এবং স্বর্ণিল। সুদূর মেসোপটেমিয়া কিংবা আরও প্রাচীন কালেও তাঁর উপস্থিতি খুঁজে পান ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিকেরা। দেবীর যুগে যুগে বিবর্তন ও সূত্রপাতের মোড়গুলিও দেবী দশভুজার মতোই উৎকর্ষতা আর কৌতূহল গবেষণায় সমান আকর্ষণীয়। ষাটের দশকে মথুরা অঞ্চলে খোঁড়াখুঁড়িতে দশভুজার যে মূর্তি উদ্ধার হয় তাতে দেবী সিংহবাহিনী, দশভুজা, দশপ্রহনধারিণী। এই মূর্তিগুলি অধিকাংশই কুশান যুগের বলা হচ্ছে।
বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতকের কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম দেবীর যে ছবি এঁকেছেন তাতে চিত্রিত হয়েছে,-মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চিণ্ডকা / সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ / মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোহণ? বাম করে ধরিলের মহিষের চুল / ডানি করে বুকে তাঁর আরোপিলা শূল / অঙ্গদ-কঙ্কন যুতা হৈল দশভুজা / যেইরূপে অবনীমণ্ডলে নিলা পূজা। কিন্তু দেখা গেছে কুশান যুগের দেবী মূর্তির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবী দশভূজার মিল পাওয়া যায় না। দুই খানেই দেবী যোদ্ধা হলেও কুশান আমলে তিনি মহিষাসুর মর্দিনী নন। বৈদিক যে সব ব্যাখ্যা বিধৃত আছে বিভিন্ন বেদে তাতেও মহিষাসুরমর্দিনীর চিত্র স্পষ্ট নয়। পুরাণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পুরাণে দেবী দুর্গার উপস্থিতি রয়েছে সেইগুলির রচনাকালে গুপ্ত যুগ বা তাঁর পরবর্তীকাল। সেই সব আখ্যানকে আলাাদ করে দেবী-মাহাত্ম্য বা দুর্গা-সপ্তশতী তৈরি করা হয়েছে, যা বাংলার শ্রীশ্রী চণ্ডী।
অর্থাৎ দেবী মাহাত্ম্য কুশান যুগের ছয়শো বছর পরে রচিত। সেই আখ্যানই মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী। বিভিন্ন পুরান, উপপুরাণে দেবীর বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই বিরোধিতাপূর্ণ। ভাগবত পুরাণে নারদ রামচন্দ্রকে রাবনবধের জন্য দুর্গা পুজো করতে বলেছেন। মহাভারতে কোথাও কোথাও দুর্গার উল্লেখ আছে। তবে মহাভারতে দেবীকে চতুর্ভুজ, বিন্ধ্যবাসিনী, মহাকালী ছাড়াও বাসুদেব ভগিনী বলা হয়েছে। মানে দুর্গা, এখানে নিদ্রাদেবী বা বিষ্ণুমায়া। এর বাইরে ভাগবত পুরাণে দুর্গাস্তব রয়েছে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন এইটি মহাভারত রচনার অনেককাল পরে এসেছে এবং পরে মহাভারতে সংযোজিত হয়। অন্যদিকে বাল্মীকি রামায়ণে দুর্গাপুজোর উল্লেখ না থাকলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে এসেছে রামের অকাল বোধনের কথা। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় মৃচ্ছকটিক নাটকে। বানভট্টের হর্ষচরিত, কালীদাসের কুমারসম্ভব রচনায় দেবী মহিষাসুরমর্দিনী রূপে না এলেও পর্বতবাসিনী রয়েছেন। শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, মহিষাসুরমর্দিনীর উল্লেখ রয়েছে প্রাচীন তামিল সঙ্গম সাহিত্যে। দেবীকে কোররাবই বলা হয়েছে তামিল ভাষায়। সব মিলিয়ে এটি স্পষ্ট দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধ ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধের কথা সারা দেশেই নানাভাবে বিবৃত আছে। দেবীর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার যোগাযোগ বা মিল রয়েছে সর্বত্র।
এই দেবী কোথাও দশভুজা, কোথাও দ্বাদশভুজা কোথাও বা ষোড়শভুজা হয়েছেন। তাঁর প্রাচীনত্ব ও প্রসার বিশাল। তিনি শুধু প্রাচীন ভারতেই নয়, উপাস্য ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। দেবীর বর্তমান রূপ গ্রহণের এবং তাঁর দুই পাশে লক্ষ্মী সরস্বতীর উপস্থিতি নিয়ে আরও বিশাল গবেষণা রয়েছে। তবে বাংলার মানুষের মনোচক্ষে দশভুজার যে পারিবারিক চিত্র তার পেছনে সেই সময়কার কবিদের কল্পনাও বিশাল কাজ করেছিল। প্রভাব ছিল বৈদিক যুগের শেষের দিকে যে ঋষিরা বেদের বহুদেবতার ওপরে উঠে একেশ্বরবাদের খোঁজ চালিয়েছিলেন-তাদের নানা কাজের। তাই তো বাঙালি মহালয়ার ভোরে উচ্চারণ করে থাকে ঋক্কেদের এক সূত্র-আমি রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্য ও বিশ্বদেবের সঙ্গে বিচরণ করি। দেবতারা আমাকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাগ করেছেন (কিন্তু আমি এক)।