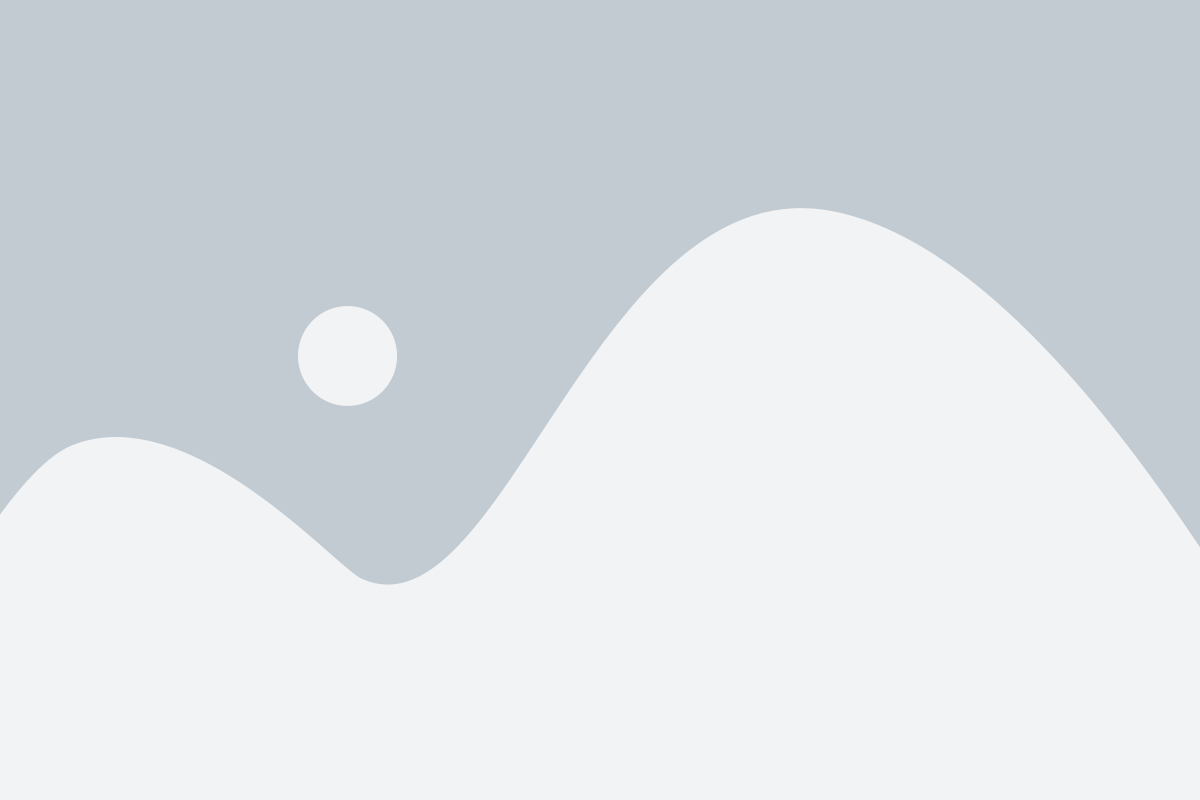ব্রিটেনে বিক্রি হবে কলকাতার টাটকা রসগোল্লা, কাঁচামাল নিয়েই রয়েছে জট!!
বাণিজ্যে বসতি!!

বাংলা ভাষার একটি চালু প্রবাদ আছে: বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।অর্থাৎ যেথায় বাণিজ্য, সেথায় মা লক্ষ্মীর বসতি।এই প্রেক্ষাপটে দেখলে আগামীকাল অথবা পরশুর প্রত্যুষ ভারতের আর্থিক আত্মার জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, সব ঠিক থাকলে ভারতীয় সময়-সারণি ধরে ৮ কিংবা ৯ জুলাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ভারতের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। ভারতের কী কী আমদানি পণ্যের উপর কত শতাংশ শুল্ক ধার্য করবে ওয়াশিংটন এবং এর পাল্টা নয়াদিল্লী আমদানিকৃত কী কী মার্কিন পণ্যের উপর কত শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে, বস্তুত এই জটেই এতদিন আটকে আছে বাণিজ্য চুক্তি। যদিও এই চুক্তি পূর্ণাঙ্গ মুক্তবাণিজ্য চুক্তি নয়, বরং সাময়িক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এমন একটি কাঠামো, যা দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের শুল্ক, রপ্তানি সীমাবদ্ধতা ও বাজার প্রবেশাধিকারের বিতর্কের অবসান ঘটানোর প্রথম ধাপ। তাই একে বলা হচ্ছে ‘ইন্টারিম ডিল’। এই চুক্তির খসড়া কাঠামো এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও ভূকৌশলগত প্রভাব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এটি শুধু বাণিজ্যসুলভ একটি কৌশল নয়, বরং দুই শক্তিধর গণতান্ত্রিক দেশের পরস্পর নির্ভরশীল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী দলিল।
প্রস্তাবিত খসড়া অনুযায়ী, ভারত বেশ কয়েকটি আমেরিকান কৃষিপণ্যে – বিশেষত বাদাম, আঙুরজাত ফল, ব্লুবেরি, গম এবং প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধজাত দ্রব্যে সীমিত ছাড় দিতে রাজি হয়েছে। এই ছাড়ের পরিমাণ এখনও পুরোপুরি প্রকাশ না হলেও সূত্র অনুযায়ী তা হবে কোটাভিত্তিক বা সুনিশ্চিত পরিমাণে শুল্ক হ্রাস। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় তৈরি পোশাক, চর্মজাত দ্রব্য, হ্যান্ডলুম, ইঞ্জিনীয়ারিং গুডস এবং কিছু তথ্যপ্রযুক্তি যন্ত্রাংশে বিদ্যমান অতিরিক্ত শুল্ক, যা পরিভাষায় ‘রিট্যালিয়েটরি ট্যারিফ’ তথা প্রত্যাঘাতমূলক শুল্ক, তা তুলে নিতে রাজি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই ইন্টারিম চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম মেনে তৈরি করা হচ্ছে। যাতে কোনও পক্ষ আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে না পড়ে। শুধু পণ্যের উপর শুল্ক নয়, এই চুক্তির খসড়ায় স্থান পেয়েছে পরিষেবা বাণিজ্য, ডিজিটাল স্ট্যান্ডার্ড, ফার্মাসিউটিক্যাল অনুমোদন প্রক্রিয়া, ডেটা স্থানান্তর এবং সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সমঝোতা। যদিও এই খাতগুলিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন, তবু এই চুক্তি এমন একটি কাঠামো তৈরি করছে, যার ভিত্তিতে আগামীতে একটি বৃহৎ ও বিস্তৃত মুক্তবাণিজ্য চুক্তির দিকে আগুয়ান হবে দুই দেশ।
এই চুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব বহুস্তরীয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে বললে, ভারতের শ্রমনির্ভর উৎপাদন ক্ষেত্র, বিশেষ করে বস্ত্র ও হস্তশিল্প, আমেরিকান বাজারে নতুন করে প্রবেশাধিকার পাবে, যা লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের জন্য উপকারে আসবে। একইসঙ্গে, আমেরিকার কৃষিপণ্য ভারতের প্রিমিয়াম বাজারে প্রবেশ করলে একদিকে যেমন ভোক্তাদের কাছে আরও পণ্যসুলভ বিকল্প তৈরি হবে, তেমনই দেশীয় কৃষি উৎপাদনের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে। ফলে সরকারকে অবশ্যই এই খাতে প্রতিক্রিয়া সামলানোর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। আবার, ভূকৌশলগত পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তির তাৎপর্য আরও গভীর। চিন যখন ‘ডি-কাপলিং’ তথা জোটহীন বাণিজ্য জোট গঠনের পথে,তখন ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠতা শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নয়, বরং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি নতুন অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করতে পারে। ভারত ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন’- এ নিজেদের স্থান সুনিশ্চিত করতে চাইছে, সেখানে আমেরিকাও চাইছে চিনের বিকল্প উৎপাদন ঘাঁটি হিসাবে ভারতকে উৎসাহিত করতে। এই চুক্তি সেই প্রক্রিয়ায় একটি বড় পদক্ষেপ।
তবে চ্যালেঞ্জ যথেষ্ট। ভারত এখনও কৃষি ও দুগ্ধখাতে আমেরিকান প্রবেশ নিয়ে সন্দিহান। যুক্তরাষ্ট্র থেকে গরুর দুধ, ছানা, প্রক্রিয়াজাত পনিরের আমদানি ভারতীয় বাজারে সস্তায় প্রবেশ করলে দেশীয় খামারিদের উপর প্রবল চাপ তৈরি হতে পারে। আবার, আমেরিকান পক্ষও ডিজিটাল অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তি নীতির ক্ষেত্রে ভারতের ‘ডেটা লোকালাইজেশন’ এবং ‘নিয়ন্ত্রক জটিলতা’ নিয়ে উদ্বিগ্ন। ফলে মধ্যবর্তী চুক্তি হলেও মূল কাঠামোগত দ্বন্দ্ব মিটতে এখনও বহু পথ বাকি। স্মরণে থাকুক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম একক রপ্তানি গন্তব্য এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম সামগ্রিক বাণিজ্য অংশীদার। অন্যদিকে, আমেরিকার ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাই এই বাণিজ্য চুক্তি শুধু রপ্তানি বা আমদানি নয়, বরং একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ। আসন্ন চুক্তিটি তাই কেবল একটি অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের বিষয় নয়, বরং বরং কৌশলগত বিশ্বাসের পরীক্ষাগারও বটে। এটি এমন এক পর্বাচহ্ন, যা বোঝায়- দুই বৃহৎ গণতন্ত্রই চাইছে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে একটি দীর্ঘমেয়াদি পথ নির্মাণ করতে। এক্ষেত্রে যদি দুই দেশ বাস্তবতা ও প্রত্যাশার মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে পারে, তবে এই চুক্তিই হতে পারে ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক স্থায়িত্ব ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তর।